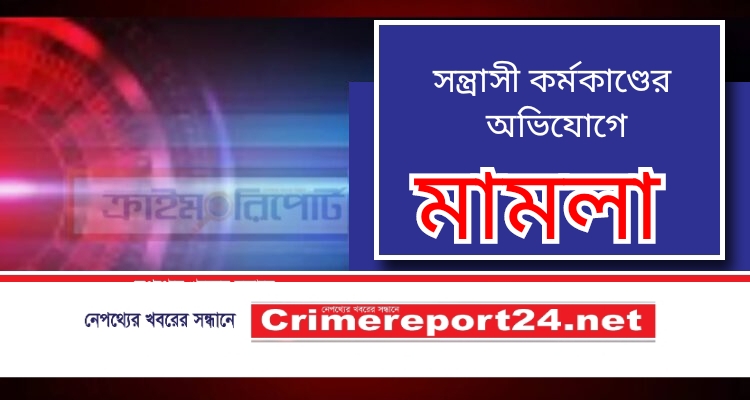রেণুর আবির্ভাব উপন্যাস থেকে


হারুন আল রশিদ
ওই বছরের ভাদ্র মাসের এক বিকালে আমি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর ভ্যাপসা গরমে গিমাডাঙ্গা স্কুলের মাঠে সতীর্থদের সাথে ফুটবল খেলছি। আমরা বাইশটা ছেলে দুই ভাগ হয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে গোলপোস্ট বসিয়ে পায়ে পায়ে লড়াই করি। আনন্দে সময় কেটে যায়। দুই চারটা ছেলে অকারণে গড়াগড়ি করে। কেউ কেউ লাফ দেয়। কেউ ডিগবাজি খায়। দুএক জন নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে। আবার সবাই ফুটবলের পেছনে দৌড়ায়। খেলা জমে ওঠে। আমাদের দলের একজন উন্মত্ত হয়ে সাদা-কালো বলটাতে কিক করে। ওটা গিয়ে প্রতিপক্ষের একটা ছেলের পায়ের কাছে পড়ে। সেই ছেলে নিজের গোল পোস্টের দিকে কিক দেয়, আর তার দলের একজনের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে মুখ কালো করে বসে পড়ে। আবার উঠে গিয়ে নিজের দলকে জেতানোর জন্য দৌড়তে থাকে।
কিছুক্ষণ ধরে আমি ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলাম। আমার পা দুটি কাঁপছিল। আমি টুঙ্গিাপাড়া গ্রামের ছেলে। চার বছর ধরে আব্বার কর্মস্থল গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়ি। টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে আসলে প্রথম রাত আমার কখনও ঘুম হয় না। সারা রাত গ্রামের কথা, গ্রামের মানুষের কথা, সতীর্থদের কথা ভাবি। ভাবলাম নির্ঘুম রাত কাটানোর ফলে হয়তো আমার এই দুর্বতলা। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও আমি অবশ্য কারও চেয়ে কম লড়ি না। ফুটবলের সাথে আমার পায়ের আশৈশব সখ্য। আমার আব্বা ফুটবল খেলা ভালোবাসেন। আমি ভালোবাসি। আমার ধারণা আমার সন্তানরাও তা-ই করবে।
আমার দল ভালো খেলে। আমারও উৎসাহ বাড়ে। এক সময় বলটা আমার পায়ের কাছে আসে। আমি ওটা নিয়ে এগিয়ে যাই। মাঠের চারিদিকে দর্শক। যাঁরা শুষ্ক থাকতে চান, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন স্কুলের বারান্দায়। অনেকে অবশ্য ভাদ্র মাসের বৃষ্টিকে বৃষ্টিই মনে করেন না। তাঁরা লাইন ধরেছেন স্কুল ঘরের বিপরীত দিকের রাস্তায়। দর্শকদের কেউ নৌকার মাঝি, কেউ দোকানী, কেউ কৃষক, কেউবা হিন্দু জোতদারের চাকর বা মুসলমান আড়তদারের কর্মচারি। তাঁরা হাততালি দেন। আমি পায়ে পায়ে বল নিয়ে দৌড়াই। এক জন আমার কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে এসে আমার বাহুর সাথে বাড়ি খেয়ে নিজেকে কোনও মতে সামলায়। এক জন আমার পেছনে পেছনে আসে। আমি তার ফোঁপানির শব্দ শুনি। সিদ্ধান্ত নিই কোনও কিছুকেই বলের উপর থেকে আমার মনোযোগ কেড়ে নিতে আমি অনুমতি দেব না। কয়েকজন আমার দুই পাশে লাফায়। অনেকটা অকারণে। আমার সব একাগ্রতা আমি আমার পায়ে জড়ো করি আর খেলতে খেলতে আমি প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের কাছে চলে আসি। তারা আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে। শৈশব থেকে অনুশীলন করে শিখেছি কী করে খেলার উত্তেজনাপূর্ণ সময় বল পায়ের কাছে রাখতে হয়। আমি তা-ই করি। আর সুযোগ বুঝে কিক করে বলটাকে একটা ছেলের মাথার উপর দিয়ে চালান করে দিই।
গোল হয়েছিল কি না, আমার জানা হয়নি। বলে কিক দিতে গিয়ে দেহের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম। তারপর আমার পা আকাশে, মাথা পাতালে, আর সব কিছু আমার চারিদিকে লাটিমের মতো ঘোরে। আমি তিন জন করিম, চার জন বাবুল, পাঁচটা গোলপোস্ট, দশটা আমগাছ, বিশটা কাঁঠালগাছ, কয়েকশত নারকেলগাছ দেখি। লম্বা স্কুলটা চারটি ঘরে পরিণত হয়ে একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমি যাদের দেখি তাদের সবারই আমার মতো অবস্থা: পা আকাশে, মাথা ভূমিতে। আমি ঘূর্ণিটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। এক সময় আমি মাটিতে পড়ে যাই।
পিঠের নিচে ভেজা খসখসে ঘাস। আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখি। টের পাই মাথা ঘোরা কমছে। কিন্তু শুরু হয় মাথা-ব্যথা। নিমেষে তা বেড়ে যায়। কপালটা কাঁপতে থাকে, বুঝি ফেটে মগজ বের হয়ে আসবে। আর যেন এক দল জ্বিন কামান থেকে আমার দুই কানে ফুটন্ত পানির গোলা নিক্ষেপ করছে।
আমি ব্যথা সহ্য করি আর অপেক্ষা করি ওটা ভোঁতা হয়ে আসার জন্য। মানুষের সামনে বমি করব না, এই প্রতিজ্ঞাও অটুট রাখি। আমার গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট কাদায় ডুবে আছে। পা দু’টি ছড়ানো। ফুসফুসে অনুভব করি বায়ু-শূন্যতা, যদিও শ্বাসপ্রশ্বাসে আমার বুক তিন ইঞ্চি করে ওঠানামা করে।
আমার চার দিকে সতীর্থ আর দর্শকের ভিড়। আমার অস্বস্তি লাগে। এমন কেন হলো? শুধু এক রাতের নিদ্রাহীনতার কারণে এটা হওয়ার কথা নয়। মাসখানেক ধরে একটু দৌড়ালে বা ও-রকম কিছু করতে গেলে আমার বুক ধপধপ করত। আবার গতি থামার কিছু সময় পর বুক শান্ত হয়ে যেত। মনে হলো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হয়নি।
আমার পায়ের কাছে কয়েকজনের কথা কাটাকাটি চলে। কী হলো? কী হলো? মৃগী রোগ? অবশ্যই মৃগী রোগ। কবে থেকে শেখের বেটার মৃগীরোগ? আগে কয় বার মূর্ছা গেছে, কে বলতে পারে? শেখ বাড়ির বয়স্ক কেউ এখানে আছে কি?
“মৃগী ট্রিগি কিছু নয়,”এক জন বলেন, “যে জোরে মজিবরের মাথায় বল লেগেছে। আমি নিজ চোখে দেখেছি।”
“যে ছেলেটা পড়ে গেছে,” অন্য এক জন বলেন। “সে মজিবরের মাথায় পিছন থেকে গদা দিয়ে মারে। মফিজ তুমিওতো দেখছ।”
মফিজ নামের লোকটা মাথা উপর-নীচ করেন।
“জিন-ভূতের আছর আছে কি না সেটা আগে জানা দরকার?”
একজন একটা চামড়ার জুতা আমার মুখের উপর ধরেন। “মজিবর, বুক ভরে গন্ধ নাও।”
“জুতা কেন? শেখের বেটার জ্ঞান আছে, দেখতেছ না?”
“এটা মৃগীরোগের আক্রমণ।”
“মৃগীর লক্ষণ কই? ও-তো কাঁপতেছেও না।”
”মুখে ফেনা কই?”
“তোমার এই পচা জুতার গন্ধে মৃগী চলে আসবে।” একজন জুতার মালিকের হাত থেকে জুতাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন।
“তোমরা সবাই সরো,” গিমাডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক তাহের স্যার বলেন। উনি দুই হাত দিয়ে লোকগুলোকে দুই দিকে ঠেলে আমার মাথার কাছের জায়গাটা ফাঁকা করেন। “মজিবরের বাতাস দরকার,” তাহের স্যার বলেন।
আমার বুকে ভাদ্র মাসের গরম বাতাস চাপড় মারে। আমি খেয়াল করি বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখি কবিগুরুর আঁকা রং। নীল আকাশে কে ভাসাল সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই, সাদা মেঘের ভেলা?
মিনিট কুড়ি পর বুক ধড়ফড় কমে আসে। আমি উঠে দাঁড়াই। অনেকে আমাকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। আমি বলি, আমি ঠিক আছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
বাড়ির পথে হাঁটা ধরি। অনেকগুলো লোক কাটা খাল পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেন। অনেক কষ্টে নৌকায় উঠি। চার বছর আগে একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকা থেকে এই খালে পড়ে গিয়েছিলাম। সে দিন এখানে এত পানি ছিল না। তারপরও বুকে বই চেপে ধরে শুধু পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করি। মাঝি আমাকে উদ্ধার করার আগে কয়েক সের পানি খাওয়া হয়ে যায়। তারপর আম্মা আর আমাকে গিমাডাঙ্গা স্কুলে যেতে দিলেন না। আমাকে আব্বার কর্মস্থল গোপালগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন।
নৌকায় আমার সাথে আরও এক ডজন ছেলে ছিল। ওরা আমাদের বিভিন্ন দরিদ্র আর জান্নাতবাসি আত্মীয়স্বজনের সন্তান, থাকে আমাদের বাড়িতে। ওদের কয়েক জন ফুটবলটার জন্য আক্ষেপ করে। আমার ফুটবল। আব্বা কিনে দিয়েছিলেন।
আমি বলি, “চিন্তা কোরো না তোমরা। আমি আব্বাকে বলব তোমাদের জন্য আর একটা বল আনতে।”
“মিয়া ভাই, কথা বোলো না,” আমার এক তৃতীয় স্তরের চাচাত ভাই বলে। “তোমার কষ্ট হচ্ছে।”
আসলেই আমার কষ্ট হচ্ছিল।
নৌকা থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে মনে হলো আর পারব না। বাড়ির ছেলেগুলো আমাকে ঘিরে রাখে। এক মাইলেরও কম পথ। মনে হলো একশ মাইল হাঁটছি। তবু বাড়ির দেখা মেলে না।
হেঁটে ভালো করিনি। বাড়ি পৌঁছে কিছুতেই শরীরের কাঁপন ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। তাই আমি সোজা খাটে চলে যাই।
বিছানার ছোঁয়ায় মনে হয়, আহা কী শান্তি। এমন সুখতো আগে কখনও অনুভব করিনি। আমার সারা শরীর শীতল হয়ে আসে। চাঞ্চল্যের বুঝি চির-বিদায় হয়। মস্তিষ্কের দ্বার খুলে যায়। কোরানের আয়াত মনে আসে। ওয়া বাশ্শিরিল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসোয়ালিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার…আর সুসংবাদ দিন তাঁদের, যাঁরা ঈমান এনেছেন। তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান।
আমার শিরায় শিরায় সে সুধা বয়ে যায়। আর ঘুম আসে। যেন আমি বেহেশতে চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। কোনও দুঃখবোধ অনুভূতিতে নাই। সব চিন্তা চলে গেছে। চিন্তাহীনতায় এত সুখ। সুখে বুঁদ হয়ে খুব দ্রুত চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার আগে আমি চোখ বন্ধ করি।
আমি সারা রাত অচেতন থাকি। চেতনা ফিরে আসার সময় ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে। মনে হলো মৃত্যু থেকে ফিরে এলাম, যেখানে কোনও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল না। আর এখন জেগে ওঠার সময় মনে হলো জন্মগ্রহণ করছি। কবর থেকে। আর মানসিক ব্যাধিগুলো ফিরে আসছে একে একে। চোখের এক একটা পাতার ওজন দশ সের। ওগুলো খুলতে গিয়ে কপালের উপর চাপ অনুভব করি। এর মধ্যে বুঝি পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। আর আমি তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের এক প্রবীণ নাগরিক। আর কখনও বিছানা থেকে উঠতে পারব না। চোখ দুটি আবার আপনা-আপনি বুঁজে আসে।
টের পাই ঘর আর উঠানে অনেক মানুষ। এক সময় আমি মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ করতে সমর্থ হই। মনে আছে আমি মাঠের ভেজা কাপড় নিয়ে বিছানায় গিয়েছিলাম। এখন আমার গায়ে পরিষ্কার পাজামা আর শার্ট। আম্মা মাটিতে বসে আছেন, আমার মাথার পাশে। তারপর আমার চোখ পড়ে রেণুর উপর।
সে দিন প্রথম রেণুকে আমি ভালোভাবে দেখি। কিছুক্ষণ ওর কটা চোখে আমার চোখ লেগে থাকে। সাদা তুলতুলে গোলগাল চেহারা। গোলাপী জামা পরে রেণু উৎসুক নয়নে আমাকে দেখে। মসৃণ ছোট একটা নাক। সাদা গাল দু’টি বুঝি কোনও পাহাড়ি ঝর্ণাধারার মসৃণ রূপ। জানালা দিয়ে সূর্যালোক এসে ওর ঘন চুলে জড়ো হয়। রেণুর পেছনে জানালার বাইরে একটা পেপে গাছ। কাছে কোথাও একটা দোয়েল পাখি ডাকে। আমার আনন্দ তখন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দ। রেণুর বয়স তখন চার। আজ বুঝি সেটা কত সৌভাগ্যের ছিল। মুরুব্বিদের দেয়া উপহার। আসলে রেণু তখন এক বছর ধরে আমার স্ত্রী।
মেজ চাচির কথায় বুঝি, আব্বা রাতেই নৌকা নিয়ে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলেন ডাক্তার আনতে। আর এক ফুফার কথায় বুঝলাম, আব্বা এখন ডাক্তারকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাচি-ফুফু-খালা আর তাঁদের স্বামী-সন্তানদের গুঞ্জন বাতাস ভারী করে। আমি ছাড়া আর সবাই আমার জন্য কষ্ট পান।
আম্মা দেয়ালের দিকে সরে যান। এক জন একটা মোড়া এনে আমার বুকের কাছে রাখেন। ধুতি পরা পৌঢ় ডাক্তার আমার পাশে বসেন। সাথে সাথে আমার কব্জি ডাক্তার বাবুর হাতের মুঠোয়। ডাক্তার বাবু চোখ বন্ধ করেন। আমি তাঁকে দেখি। আমি দেখি সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তার বাবু আমার কব্জি ছেড়ে দেন। তিনি আমার চোখের পাতা উল্টে ভেতরটা ভাল করে দেখেন। তারপর আমার আর ডাক্তার বাবুর চোখাচোখি হয়। ডাক্তার বাবুর মুখের তৈলাক্ত কালো রঙে নীল আভা যুক্ত হয়। বুঝলাম আমাকে দেখে তিনি চিন্তিত হয়েছেন।
ডাক্তার বাবু তাঁর কালো ব্যাগটা টেনে কোলের উপর নেন। আমি বেগের চেইন খোলার শব্দ শুনি। তিনি ব্যাগ থেকে স্যালাইন, পাহপ, ক্লিপ, ফিতা, আর চারটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বের করে খাটের উপর রাখেন। তারপর আমার ডান হাতের পিঠের রগে সুঁই ঢোকান। মোটা মানুষের অবিচল দক্ষ হাত। ডাক্তার বাবু দাঁড়িয়ে স্যাালইনটা খাটের উপর মশারি টাঙানোর বিমের সাথে ঝুলিয়ে দেন। পাইপটা সেলাইনের থলেতে ফিট করেন, পাইপের উপর চাকাটা ঘুরিয়ে স্যালাইনের ফোঁটা নিয়ন্ত্রণ করেন। টপটপ করে ফোঁটাগুলো পড়ে পাইপের মাথায় ঢেঁড়স সাইজের খাপটাতে জমা হয়।
কাজ শেষ করার পর ডাক্তার বাবু একটা নিশ্বাস ফেলেন।
সূঁচ থেকে রগ দিয়ে স্যালাইন-পানি আমার ভেতরে প্রবেশ করার অনুভূতি আমি ধরতে পারি। আমি পানির ধারাটা খেয়াল করতে থাকি। বুঝতে পারি তা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমার একটু একটু ভাল লাগছে। আমি আমার অনুভব সেলাইনের ধারায় কেন্দ্রীভূত করি। বুঝতে পারি আমার শরীরে ক্ষীণ ধারার প্রাণের সঞ্চার ঘটে চলেছে। আমার আর ডাক্তার বাবুর আর এক বার চোখাচুখি হয়। তিনি আর একটা নিশ্বাস ফেলেন। আমি দেখি তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে। আর বুঝি ওটা ছিল স্বস্তির নিশ্বাস।
আমার হাতে সেলাইনের সুঁই লাগানো অবস্থায় ডাক্তার বাবু দুই ঘণ্টা ধরে হৃদ্বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমার বুক ও পিঠ পরীক্ষা করেন। ওই দুই ঘন্টা আমার আব্বার চোখ আমার উপর থেকে সরে না। আমার চোখ বার বার আম্মাকে খোঁজে, কিন্তু পায় না। ডাক্তার বাবু কান থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে হাতে ধরেন, আর বলেন, “আমি তো তেমন কিছু পেলাম না।”
ডাক্তার বাবুর কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের আভাস নাই। আমি চোখ ঘুরিয়ে দেখি অন্যদের চোখেও উদ্বেগ। নারীরা সরে পেছনে চলে গেছে। আমি শুধু পুরুষদের দেখি। আব্বার চোখ আমাকে দেখে। তীক্ষ্ণ গভীর চোখ। আব্বার প্রশস্ত কপাল টানটান হয়ে আছে। তিনি আমার থেকে চোখ সরিয়ে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে তাকান।
“ও কি ভালো আছে, ডাক্তার বাবু?” আব্বা কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।
ডাক্তার বাবু উত্তর করেন না।
“চুপ করে আছেন কেন, ডাক্তার বাবু?” আব্বা বলেন। “কেন কথা বলছেন না?”
“আর এক বার দেখি,” ডাক্তার বাবু বলেন।
ডাক্তার বাবু হৃদ্বীক্ষণ যন্ত্রটা আর এক বার কানে লাগান। যন্ত্রের ডায়াফ্রামটা আবার আমার পাজরের উপর চেপে ধরেন। পনেরো মিনিটের উপর তিনি আমার বুক আর পিঠ অনুভব করেন। পেটের উপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেন। পিঠেও। তারপর তিনি আবার যন্ত্রটা বিছানার উপর রাখেন।
“আমার ছেলে যে জ্ঞান হারিয়েছে, ডাক্তার বাবু,” আমার আব্বা বলেন।
আমি কারও ফোঁপানির আওয়াজ শুনি। তবে তা আমার আম্মার শব্দ নয়।
“সেটাই ভাবছি,” ডাক্তার বাবু বলেন।
আমি আমার আব্বাকে দেখি। তাঁর দুই কাঁধ শক্ত হয়ে ছিল। এখন তিনি ওগুলো ছেড়ে দিলেন। যেন আমার আব্বা নিজের মধ্যে ফিরে এসেছেন।
“ডাক্তার বাবু, খুলে বলেন। যা পেয়েছেন, তা-ই বলেন।”
“উপসর্গ দেখে মনে হচ্ছে হার্টে এক বা একাধিক ছিদ্র আছে।”
আমার চোখ জনতার দিকে ঘোরে এবং তারপর আমার আব্বার চোখের সাথে মিলিত হয়। উপস্থিত মান্যগণ্যগণ একে অপরের দিকে তাকান। সবচেয়ে বেশি তাকান আমার দিকে। তাঁদের দৃষ্টি দেখে মনে হয় আমার গালের এক দিক বুঝি পুড়ে গেছে। যেন তাঁরা আগে আমাকে কখনও দেখেননি। তারপর এক সাথে অনেকগুলি নিশ্বাসের শব্দ শুনি। এক জন কথা বলে ওঠেন।
কী? ছিদ্রি?
এটা আবার কী?
কখনওতো এ রোগের নাম শুনিনি।
কী অসুখ এটা?
আমি শুনেছি।
কী?
কী, বোঝো না?
না, বুঝি না।
আরে গাধা। ফুটা, ফুটা। হার্টে ফুটা।
কীসের ফুটা? কেমন করে এটা হয়?
মজিবরের হার্ট ফুটা হলো কী করে?
হার্ট ফুটা হলে কী হয়?
“রোগী যে কোনও সময় মাথা ঘুরে পড়ে মরে যায়, ” ডাক্তার বাবু বলেন।
তাঁর কথা শুনে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।
সবাই আল্লাহকে ডাকেন। ঈশ্বরের নামও শুনা যায়। চাচি-ফুফুদের আর্তচিৎকার আমার কানে বাজে। আমার মন খারাপ হয়। সবাই আমাকে কত ভালোবাসেন।
আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমি বাঁচব না। এ রকম সময়ে ভয়ে হয়তো আমার চেতনা আর একবার চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিংবা আমার উচিত ছিল নীরবে কাঁদতে কাঁদতে অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার দুুঃখকে ভারী করে তোলা। আমি কোনওটাই করিনি।
আমার ভাবনা বিদ্ধ ছিল অন্য জায়গায়। মনের মধ্যে বিষয়টা বার বার উঁকি দিচ্ছিল। এক সময় আমি তার সূত্র খুঁজে পাই। আমি যে তখন কত দুর্বল আমি শরীরটা একটু ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে বুঝি। ঝাঁকুনিটা আমার দরকার ছিল, আমার বোধশক্তি ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য। আমি নিজেকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা ঠিক কি না। এত অল্প বয়সে এত কঠিন ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব কি না? আমি নিজেকে প্রশ্ন করে চলি। আর বার বার একই উত্তর পাই। তারপরও এত অল্প বয়সে আমার এত বড় মুক্তি ঘটে গেল তা আমি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি সময় নিই।
এর পর আট বছর চলে গেছে। এই আট বছরে সেই মুক্তির ব্যাপারে আমার কোনও দিন এক বিন্দু সন্দেহ মনে আসেনি। আর এখন আমি যত চাই তত বার আনন্দের সাথে নিজের কাছে ঘোষণা দিতে পারি: সেই আট বছর আগে আমি মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। এবং তা সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকালের জন্য।
আর এভাবে আমি সে-দিন জীবনের এক অলঙ্ঘ্য সমস্যা অতিক্রম করেছিলাম। চেতনাহীন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা সম্ভব ছিল কি না, জানি না। এই নির্ভীকতার যে অপরিসীম প্রভাব আমার জীবনে, তা-ও আমি ধীরে ধীরে বুঝেছি। এক সময়ে এসে জানলাম, চূড়ান্ত বিচারে, মৃত্যু-ভয়ই পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট সকল দুঃখের আদি কারণ। মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত নয়, এ রকম মানুষ আমার এই বাইশ বছরের জীবনে খুব কম দেখেছি। সেই বিমূর্ত অভয় আমার জীবনের এক অনুপম ক্ষমতা হিসাবে আবির্ভূত হয়, সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, যাদের ধ্বংস করাকে আমি আমার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছি। আজ এ কথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নাই, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারার মানে হলো জীবনের পূর্ণতা লাভ করা। আট বছর আগে, যখন ডাক্তার বাবু আমার মৃত্যু-বার্তা দিয়ে দিলেন, তখন এই অভয় আমাকে সুখ না দিলেও অনেক শান্তি দিয়েছিল।
সূত্রঃ লেখকের ফেজবুক পাতা থেকে সংগ্রহ